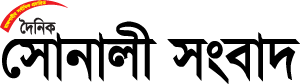যে ঋণ পরিশোধ না করাই ভালো

নজরুলজয়ন্তী
|সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী|
ঋ ণ তো আছে; থাকবেই। ক্ষুদ্রঋণ যাঁদের, তাঁরা সেটা শোধ করেন। বড় ঋণীরা তা করতে চান না। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আমাদের অনেক ঋণ আছে যেগুলো শোধ করা কখনোই সম্ভব নয় এবং সেগুলো আমাদের নত না করে ধনী করে। এমনি একটি ঋণ আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের কাছে। এই ঋণটি সাংস্কৃতিক।
সংস্কৃতির ভেতর অনেক কিছু থাকে। শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য তো বটেই; মতাদর্শও থাকে। আর ওই মতাদর্শের ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্বহীন নয়। ওইখানে, মতাদর্শের ওই জায়গাতে নজরুল ছিলেন একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী। দুই বিরোধিতার এই মিলনটা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে না, যা নজরুলের বেলাতে চমৎকারভাবে ঘটেছিল।
ব্রিটিশ শাসনকালে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতার ঐক্য ঘটা কঠিন ছিল। ব্রিটিশের কূটচাল তো ছিলই; হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বিত্তবান নেতারা– ঠাট্টা করে নজরুল যাদের টিকিওয়ালা ও দাড়িওয়ালা বলেছেন; বলেছেন রামছাগল ও খোদার খাসি, তারাও তৎপর ছিল।
ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ধর্ম ঢুকে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে। জন্ম দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। পরিণতিতে সাতচল্লিশে যা ঘটেছে তা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নয়। সেটা হলো মারাত্মক দেশভাগ।
নজরুলের নানা পরিচয় আমরা জানি। তিনি বিদ্রোহের কবি, আবার প্রেমেরও কবি। গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন। অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে। রাজনীতিতে ছিলেন। বক্তৃতা, ভাষণ, অভিভাষণ– কোনো কিছুতেই উৎসাহের অভাব ছিল না। সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন।
কারাভোগ করেছেন কবিতা লিখে; কারাগারে অনশন করেছেন। ১৯২৩-এ, বয়স যখন ২৪, তখন জেলে গেছেন। ১৯৩১-এ আবারও যেতেন, যদি গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হতো। নজরুল কিশোর বয়সেই যুদ্ধে গিয়েছিলেন, সৈনিক হিসেবে। অসাধারণ মানুষ একজন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে এই, তিনি খাঁটি বাঙালি এবং বিশ্বাসী ছিলেন সমাজ বিপ্লবে।
১৯২৯ সালে, নজরুলের বয়স যখন মাত্র ৩০, কলকাতায় তাঁকে যে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়, তাতে অন্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুও বক্তৃতা করেছিলেন। সুভাষ বসু বলেছিলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধে যাব– তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, সেখানেও নজরুলের গান গাওয়া হবে।’
তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালি যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি কারাগারে নজরুলের গান গেয়েছে। তবে সুভাষ বসুর সঙ্গে নজরুলের একটা পার্থক্যও রয়েছে। সুভাষ বসু খাঁটি বাঙালি হয়েও সারা ভারতবর্ষের রাজনীতি করেছেন। আর নজরুল ছিলেন বাংলার।
ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার যুদ্ধে নজরুল তো তিনি ছিলেনই, যে কারণে তাঁর অনেক বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং তাঁকেও কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি যে একটি স্বতন্ত্র জাতি– এই সত্যকে নজরুল যেভাবে জানতেন ও মানতেন, সুভাষ বসুর পক্ষে সেভাবে জানা ও মানা সম্ভব হয়নি। সুভাষ ও নজরুল উভয়েই চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরাগী ছিলেন।
চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে তাঁরা দু’জনেই অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন– বাঙালির রাজনীতিকে বাঙালির হাতেই রাখতে হবে; সর্বভারতীয় নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। যে জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল বাঙালির জন্য নিজস্ব রাজনীতি গড়ে তোলা। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যু হলে বাংলাকে স্বতন্ত্র রাখার আশা লুপ্ত হয়ে যায়।
সর্বভারতীয় রাজনীতির দুই ধারা– কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বারা বাহিত হয়ে এসে বাংলার রাজনীতিকে নিজেদের অংশ করে ফেলে এবং সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত উগ্র হতে থাকে। সুভাষ বসুর পক্ষেও চিত্তরঞ্জনের পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার উপায় থাকেনি। তিনি বাংলার নয়; সারা ভারতের নেতা হয়েছেন।
১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার পর থেকে পাকিস্তানের দাবি প্রবল হতে থাকে। বাংলা যে শেষ পর্যন্ত দু’ভাগ হয়ে যাবে, তার আশঙ্কাও প্রবল হয়ে ওঠা শুরু করে। নজরুল অবশ্যই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। চরম পরিণতিটি তিনি দেখে যাননি। কিন্তু আশঙ্কা করেছেন, যে জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধেই বলেছেন। ১৯৩১ সালে ‘নবযুগ’ পত্রিকায় তাঁর নিজস্ব কৌতুকবোধসহ তিনি লিখেছেন, ‘এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ মুক্ত হল না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঢুঁস মারে। দেখে হাসি পায়।’
এই দুই পক্ষের স্বার্থে ও তৎপরতায় দেশ যখন সত্যি সত্যি ভাগ হয়ে গেল, নজরুল তখন অসুস্থ। সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই কঠিন দুঃখ পেতেন। ১৯৪২-এ ‘নবযুগে’ই তিনি লিখেছিলেন, “বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– ‘বাঙালির বাংলা’ সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে।” আরও লিখেছেন, “বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে যে মন্ত্র শেখাতে হবে তা হলো বাংলাদেশ আমাদের, এখান থেকে আমরা তাড়াব পরদেশী দস্যু ও ডাকাতদের, রামা’দের গামা’দের।” বোঝা যাচ্ছে, রামা-গামা বলতে বুঝিয়েছেন অবাঙালি ব্যবসায়ীদের। ওই লেখাতে যে ধ্বনিটি নিয়েছিলেন সেটি হলো– ‘বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।’ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের বাঙালিকে ওই ধ্বনি দিতে হয়েছে এবং যুদ্ধে গিয়ে স্বাধীন করতে হয়েছে বিভক্ত বাংলার পাকিস্তানি অংশকে।
কাজী নজরুল ইসলাম (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬-১২ ভাদ্র ১৩৮৩)
জাতীয়তাবাদের জন্য রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাংস্কৃতিক ঐক্য। ওই লক্ষ্যে নজরুল যেভাবে কাজ করেছেন, অন্য কোনো বাঙালি সংস্কৃতিসেবী তেমনভাবে করতে পারেননি। হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তিনি একটি ধারায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। ইবরাহীম খাঁকে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেছেন যে, কাজটি তিনি সচেতনভাবেই করেছেন।
তাঁর বক্তব্য ছিল– ‘বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্যপ্রচলিত মুসলমানি শব্দ দেখে ভ্রু কুঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।’
নজরুলের সৌন্দর্যবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও উঁচুমানের। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্যের চেয়েও সংস্কৃতির ঐক্যকে তিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। হিন্দু দেবদেবীর নাম নেওয়ার অপরাধে তাঁকে ‘কাফের’ বলা হয়েছে। অন্যদিকে তথাকথিত মুসলমানি শব্দ ব্যবহারের কারণে তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচছেন, এমন ঠাট্টাও করা হয়েছে। নজরুল দমেননি।
তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। যে জন্য আমরা বাঙালিরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। পাকিস্তানি দুর্বৃত্তরা চেষ্টা করেছিল তাঁর রচনা থেকে তাদের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দেবে; পারেনি। নজরুল নজরুলই রয়ে গেছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছেন।
কিন্তু কেবল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী তো নন; আরও বেশি অগ্রসর চিন্তার মানুষ ছিলেন এই বিপ্লবী কবি।
নজরুল সমাজ বিপ্লবের সাংস্কৃতিক দিশারি ছিলেন। তিনি জানতেন, কাজটা তাঁর একার নয়। যে জন্য সবাইকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন ওই কাজে যোগ দিতে। কিন্তু দেখলেন, কাজটা এগোচ্ছে না। সাম্প্রদায়িকতার ভয়ংকর দানব মানুষকে বিভক্ত করে ফেলছে। যে বামপন্থিদের ওপর তাঁর ভরসা ছিল, তাঁরাও তেমনভাবে এগোতে পারছেন না।
শারীরিক মৃত্যুর ৩২ বছর আগেই যে তিনি মানসিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তার পেছনে পারিবারিক শোক ও ব্যক্তিগত অভিমান কাজ করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সমাজ এগোচ্ছে না– এই বেদনাবোধও কার্যকর ছিল; এমনটা ধারণা না করার কারণ নেই। তিনি একাকী হয়ে পড়েছিলেন। গানের জগতে আশ্রয় খুঁজেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো মানুষের একাকিত্বের বিচ্ছিন্নতা কতটা সহ্য করা সম্ভব? যে জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।
নজরুলের কাছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঋণটি কখনোই শোধ করা যাবে না। আর তেমন চেষ্টা করাটাও অপ্রয়োজনীয়। বরং যা দরকার তা হলো ওই ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উপায় একটিই। তাঁর কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া, যেটা আমরা করতে পারছি না এবং পারছি না বলেই আমাদের দুর্দিনের অবসান ঘটছে না।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সোনালী/জেআর